ঘটনার পেছনের মেয়েটি কে? : সাইফুর রহমান
প্রকাশিত:
১৭ নভেম্বর ২০১৯ ১৯:২২
আপডেট:
৪ মে ২০২০ ২০:৫৪

‘ভবঘুরে ও অন্যান্য’ নামে প্রখ্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর একখানা বই আছে। সেখানে তিনি একটি গল্পের অবতারনা করেছেন। একদা ফরাসী দেশে নাকি একজন বিচারপতি ছিলেন। খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি যাই ঘটুক না কেন শুনানীর সময় তিনি জিজ্ঞেস করতেন- মেয়েটা কোথায়? ‘শের্শে লা ফাম্’ অর্থাৎ মেয়েটাকে খোঁজো! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, পৃথিবীতে যত খুন খারাপি কিংবা অপকর্মই ঘটুক না কেন এর পেছনে একজন মেয়ে থাকবেই। আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী কোনো না কোনো ভাবে তাকে আদালতে স্বশরীরে হাজির না করা পর্যন্ত সেই মোকদ্দমার কোনো সুরাহা হবে না। একবার একটি ইনস্যুরেন্স মামলার শুনানীতে দেখা গেল একজন চিমনি পরিদর্শক একশো ফুট উঁচু থেকে পড়ে মারা যায়। হাকিম যথারীতি বলে উঠলেন ‘শের্শে লা ফাম্’ অর্থাৎ মেয়েটাকো খোঁজো। ফরিয়াদির আইনজীবী বললেন- হুজুর এই মোকদ্দমার মেয়ে খোঁজাখুজির প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? হাকিম দমবার পাত্র নয়। সেল্লাসে বললেন- খোঁজো ভাল করে। পাবে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর দুঁদে আইনজীবী মনে মনে ভাবলেন এই তো সুযোগ। তিনি বললেন- ধর্মাবতার আমাকে কয়েকটাদিন সময় দিন আমি সেই মেয়েটিকে খুঁজে বের করছি। ঝাঁনু আইনজীবী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানতে পারলেন একশো ফুট উপরে চিমনি পরিদর্শক যখন কাজ করছিলেন তখন নিচে হেঁটে যাচ্ছিলেন একজন সুন্দরী তরুণী। পরিদর্শক বেচারা নাকি ওই মেয়েটাকে দেখতে গিয়েই পা পিছলে পড়ে যায় নিচে। অবশেষে পাওয়া গেল ঘটনার পেছনের মেয়েটিকে।
এ গল্পটি বললাম এ কারণে যে আমাদের দেশে যা কিছুই ঘটুক না কেন এটাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা সবসময়ই চলে। সেটা মিন্নি কিংবা নয়নবন্ড বলে কোন কথা নয়। প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবানদের বাঁচাতে একটি গোষ্ঠি সবসময় থাকে তৎপর। ২০১৬ সালে সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের স্নাতক ছাত্রী খাদিজা বেগমকেও বদরুল নামের জনৈক ছাত্রলীগ কর্মী যখন চাপাতি দিয়ে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেছিলো তখনও আমরা দেখেছি এক শ্রেণীর মানুষ বদরুল খাদিজার সম্পর্ককে ইঙ্গিত করে নৃশংস সেই ঘটনা ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা হয়েছিলো। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এসব অপচেষ্টা হয় সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে। এগুলো কিন্তু অনেক পুরোনো কৌশল। জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিতেই এ সমস্ত কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় তাদের। রোমান যুগে সম্রাটগণ বিশাল আকৃতির এরেনাতে (স্টেডিয়াম) গ্লাডিয়েটরদের (বন্দি দাস যোদ্ধা) দুর্ধর্ষ সব লড়াইয়ের আয়োজন করতেন। প্রসঙ্গক্রমেই মনে পড়ে গেল মার্কাস অরিলিয়াস নামে একজন প্রজাবৎসল, দয়ালু ও দার্শনিক সম্রাট ছিলেন। সমগ্র রোমান ইতিহাসে যে দু’চারজন ভালো ও দয়ালু সম্রাট ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই মার্কাস অরিলিয়াস। তাঁর লিখা একটি বই আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বইটির নাম ‘মার্কাস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা’। খুবই চমৎকার একটি বই। পাঠকবৃন্দ চাইলে বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তো সেই সুযোগ্য সম্রাটের একটি অপদার্থ পুত্র ছিলো নাম, কমোডাস (১৬১ খ্রিষ্টাব্দ-১৯২ খ্রিষ্টাব্দ)। পিতা যেমন ছিলেন সুশাসক, প্রজাবৎসল ও দয়ালু। পুত্র একেবারে ঠিক তার উল্টো। ফলে কমোডাসের রাজত্বে দেখা দিয়েছিলো শুরু হয়েছিলো দুর্ভিক্ষ, দুঃশাসন, মহামারি প্রভৃতি উপসর্গ। রোম সম্রাজ্যের অবস্থা এতোটাই শোচনীয় যে গ্লাডিয়েটরের লড়াইও যথেষ্ট ছিলোনা যে প্রজাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া যায়। তো কি করা যায় এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে স্বয়ং সম্রাট কমোডাস নিজেই তলোয়ার হাতে নেমে পড়লেন সেই এরেনায় গ্লাডিয়েটরদের সঙ্গে লড়াই করতে। দুঃখ-কষ্ট, পেটে ক্ষুধা, দুঃশাসন এসব ভুলে, পেটে পাথর চেপে দলে দলে প্রজারা ছুটলেন সম্রাটের তলোয়ার চালনা দেখতে। কি আশ্চর্য! অমিত শক্তিশালী কোন যোদ্ধাই এঁটে উঠছে না স¤্রাটের সঙ্গে। সিরিয়া, বাগদাদ, গল (ফ্রান্স) আফ্রিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বন্দি দাস হিসেবে নিয়ে আসা বাঘা বাঘা যোদ্ধারা একে একে সব মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ছে সম্রাটের তলোয়ারের সামনে। প্রজারা সব বিস্ময়াবিভূত চিত্তে ভাবতে লাগলেন তাদের সম্রাট যে এতোটা বীরপুরুষ সেটা তারা কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু এভাবে প্রজাদের আর কতদিন বুদ্ধু বানিয়ে রাখা যায়। অবশেষে একদিন বেরিয়ে এলো সম্রাটের জোচ্চুরির কাহিনি। সম্রাটের লোকজন নাকি কৌশলে লড়াইয়ের পূর্বেই খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে বশিভূত করে রাখত সেসব যোদ্ধাদের। তারপর লড়াই চলাকালিন একটা সময় যখন বিষক্রিয়া শুরু হতো তখন সুযোগে সম্রাট কমোডাস তলোয়ারের আঘাতে মন্ডুপাত করতেন সেসব যোদ্ধার।
যতই দিন যাচ্ছে ততোই হত্যা, খুন, নৃশংসতা যেন ডালপালার মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একটা মহামারির রূপ ধারন করেছে। ১৫ আগষ্ট দৈনিক যুগান্তর অনলাইন সংস্করণ বাংলাদেশে প্রতিদিন সংগঠিত খুনের একটি হিসেব দিয়েছে। পত্রিকাটি লিখেছে- পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের গত ৩ মাস ২৬ দিনে সারা দেশে খুন হয়েছেন ১ হাজার ২১৫ নারী-পুরুষ। সে হিসাবে প্রতিদিন গড়ে খুনের শিকার হয়েছেন ১১ জন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সারা দেশে ২৬৭টি, ফেব্রুয়ারিতে ২৯১টি, আর মার্চে ৩০৭টি খুনের ঘটনা ঘটে। আর জুলাই মাসের ২৬ দিনে সারা দেশে খুনের ঘটনা সাড়ে ৩শ’ ছাড়িয়ে গেছে।
এর পেছনে অবশ্য বেশ কিছু কারণ নিহিত আছে। প্রথমত, বাংলাদেশে আইনের শাসন খুবই সকীর্ণ। একটি দেশে যখন ‘রুল অফ ল’ বলে কিছু থাকেনা তখন হত্যা, খুন, গুম, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি হবে এটা তো অতি স্বাভাবিক। ২০০১ সালের ২৩ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী সীমা বানু সিমিকে উত্যক্ত করার কারণে আত্মহত্যা করে সিমি। ঘটনার ১৮ বছর পেরিয়ে গেলেও মামলাটির এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়নি। বিশ্বজিৎকে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল সন্ত্রাসী কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করলো। সেই আসামিদের মধ্যে অনেকে আজও পলাতক। অন্যদিকে আইনের ফাঁক ফোকড় গলে খালাস পেয়ে গেছে অনেকে। মানুষ আর কত বলবে- বিচার চাই! বিচার চাই! বিচার চাই! দ্বিতীয়ত, মানুষ এখন ভিষণ রকম আত্মকেন্দ্রীক হয়ে উঠেছে। নিজেকে ছাড়া আর নিজের স্বার্থ ছাড়া এককদম পা ফেলতেও রাজি নয় তারা। চারদিকে সেলফির জয়জয়কার দেখলেই বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা যায়। মানুষ এখন কষ্ট না করেই সেলেব্রেটি হতে চায়। যেখানে মানুষ, কোন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার দেখালে তড়িৎগতিতে সেখানে পৌঁছে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার রুখে দাঁড়ানোর কথা সেখানে মানুষ বর্তমানে সেলফোন দিয়ে নৃশংস সেসব দৃশ্য ধারণ করে, ফেসবুক, ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছে। বেশীরভাগ মানুষেরই এখন প্রধান ধান্দা কি করে ভাইরাল হওয়া যায়। এন্ডি ওয়ারহল নামে একজন আমেরিকান লেখকও চিত্র শিল্পী সেই ১৯৬৮ সালে সুইডেনের স্টকহোমের একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন- সামনে এমন দিন আসবে যখন পৃথিবীর সবাই ১৫ মিনিটের জন্য সেলেব্রেটি হবে। যদিও তখন ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব এসব কিছুরই জন্ম হয়নি। কিন্তু কি করে তিনি চিন্তাচেতনায় এতোটা দুরদর্শী ছিলেন, ভাবলেই অবাক হতে হয়। শিল্পী ও লেখক বলেই হয়তো তার দৃষ্টি ছিলো সুদূর প্রসারিত। কিন্তু আমার প্রশ্ন ১৫ মিনিটের সেলেব্রেটি হয়ে একজন মানুষের কি লাভ। বাংলাভাষায় একটি শব্দ আছে- ‘টেকসই’। টেকসই উন্নয়ন, টেকসই গণতন্ত্র, টেকসই সাফল্য ইত্যাদি। একজন মানুষকে যদি কোন না কোন ভাবে ১৫ মিনিটের জন্য সেলেব্রেটি হতে হবে তাহলে টেকসই শব্দটির আর মাহাত্ম রইল কই। তৃতীয়টি হলো- বর্তমানে আমাদের মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যচর্চার দারুন প্রাদুর্ভাব। বর্তমান সমাজে শিল্প ও সাহিত্যেরচর্চা একেবারে নেই বললেই চলে। আর একারণেই নয়নবন্ড, বদরুলের মতো নির্মম ও নির্দয় মানুষের জন্ম হয় এই সমাজে। একসময় আমাদের সমাজে কি পরিমাণ শিল্প সাহিত্যেরচর্চা হতো তার দু’একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি আরো জোরালো ভাবে স্পষ্ট হবে। প্রথমেই বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে দু’চার কথা বলি। পাঠশালার পাঠ শেষ করে সবেমাত্র বিভূতিভূষণ হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। ঠিক তখনই পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারালেন। বিভূতির মা তাঁদের পরিবারের অন্য ছোট ছোট ভাই-বোন নিয়ে সুরাতিপুর বাপের বাড়ি চলে গেলেন। বড় ছেলে বিভূতি কী করবে? পড়ার পাঠ সাঙ্গ করে ফিরে যাবে গ্রামে? না, কিছুতেই না।
বোর্ডিংয়ে খরচ চালাচ্ছেন সহৃদয় প্রধান শিক্ষক চারুবাবু। চারুবাবু জানেন, অতি মেধাবী ছাত্র বিভূতি। কিন্তু চারুবাবু বিভূতিকে পছন্দ করেন অন্য কারণে। নানা রকম বই পড়তে পছন্দ করেন বিভূতি। চারুবাবু বিলক্ষণ বুঝতে পারেন, এই ছেলে জীবনে সফল হবেই। চারুবাবুর সুপারিশে ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বিভূতির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হলো, তবে শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, বিভূতিকে ডাক্তার সাহেবের ছেলে জামিনীভূষণ এবং মেয়ে শিবরানী-এই দুজনকে পড়াতে হবে। বিভূতিভূষণ সানন্দে সেই সব শর্তে বাড়িতে থাকতে রাজি হয়ে গেলেন। বিধু ডাক্তারের বাড়ির পাশেই মন্মথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। আর এই বাড়ির একটি নতুন আকর্ষণ হলো এখানকার একটি ক্লাব, নাম-‘লিচুতলা ক্লাব’। এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মন্মথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজেই শুধু সাহিত্য রচনা করেন না, উপরন্তু ‘বালক’ ও ‘যমুনা’ নামের দুটি সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। বিভূতিও অবিলম্বে সেগুলোর অনুগ্রাহক হয়ে গেলেন। একেকটি সংখ্যা লিচু ক্লাবে আসতেই গোগ্রাসে তার প্রতিটি লেখা পাঠ, আলোচনা, বিচার চলতে থাকে পুরোদমে।
বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু শৈশব ও যৌবন কাটিয়েছিলেন ঢাকার পুরানা পল্টনে। স্কুল জীবনে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা মিলে শুধুমাত্র হাতে লিখে প্রকাশ করতেন ‘প্রগতি’ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা। চিন্তা করে বিস্মিত হতে হয় যে শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি কতটা আত্মত্যাগ ও অনুরাগ থাকলে শুধুমাত্র হাতে লিখে টানা দু’বছর একটি পত্রিকা প্রকাশ করার মতো মহৎ কাজে ব্যাপৃত থাকা যায়। বুদ্ধদেব বসু তার আত্মজীবনী ‘আমার যৌবনে’ লিখেছেন- ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষাতে মেধা তালিকায় ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পেলাম। এতে করে মাসিক ২০ টাকা করে বৃত্তি মঞ্জুর হলো। বন্ধুরা মিলে স্থির করা গেল, হস্তলিপি-পত্রিকা আর নয়, এবারে একটি মুদ্রাযন্ত্র নিঃসৃত দস্তুরমাফিক মাসিকপত্র চাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত নেবার মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাসের কোনো এক দিনে আমার এবং কবি ও অধ্যাপক অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায়- এবং প্রধানত এই দু-জনেরই আর্থিক দায়িত্বে-‘প্রগতি’-র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম রচনা অচিন্ত্যর একটি অষ্টাদশপদী কবিতা ও জীবনানন্দর একটি কবিতা। প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিল, মনে পড়ে, বেশ একটু চা ল্যও তুলেছিলো। একদিকে এই পত্রিকা চালাবার উত্তেজনা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন জীবন-আমার দিনগুলি দুই ধারায় উচ্ছল ব’য়ে যাচ্ছে।
এবার নাটক প্রসঙ্গে একটু বলি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধির জীবন, আদর্শ ও কর্ম দ্বারা দারুন ভাবে প্রভাবিত। তো সেই গান্ধির জীবন ও আদর্শ থেকেই একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কৈশোরে মহাত্মাগান্ধি বই ও নাটক দ্বারা দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তার আত্মকথায় লিখেছেন- “বাবার কেনা একটি বইয়েরর প্রতি আমার নজর পড়ে। বইটির নাম ছিল শ্রবন পিতৃভক্তি নাটক। নাটকটি আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে প’ড়ে ফেলি। এইসময় রাজকোট শহরে একদল ভ্রাম্যমান ছবি দেখানেওয়ালা এসেছিল, একটি ছবি ছিল শ্রবণ কাঁধে ভার বেঁধে, তার অন্ধ মা-বাবাকে ব’য়ে নিয়ে চলেছে তীর্থযাত্রায়। সেই নাটকের বই ও এই ছবিটি আমার মনে গভীর দাগ কাটে। আমি মনে-মনে বলেছিলাম, শ্রবণের আদর্শে নিজেকে গ’ড়ে তুলব। শ্রবণের মৃত্যুতে তার মা-বাবার শোকে উচ্ছ্বাস আমি এখনও ভুলতে পারিনি। সেই শোকগাঁথার করুণ সুর আমায় গভীরভাবে অভিভূত করেছিল; মনে আছে বাবার দেওয়া একটি মাউথ অর্গ্যানে আমি সেই সুর বাজাতাম।
আরেকটি নাটক নিয়েও আমার অনুরূপ অভিজ্ঞতা ঘটে। ঠিক ওইসময়েই কোনো নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনীত একটি যাত্রা বাবার অনুমতি নিয়ে আমি দেখি। এই হরিশ্চন্দ্রের পালা আমার মন অধিকার ক’রে রেখেছিল অনেকদিন ধ’রে। মনে হ’ত, বারবার দেখলেও আমার চোখ যেন ক্লান্ত হবে না। কিন্তু যাত্রাগান দেখার ছুটি কি আর ঘন-ঘন মেলে? হরিশ্চন্দ্রের পালায় আমি দিনের পর দিন আবিষ্ট হয়ে থাকতাম। কতদিন যে আমি মনে-মনে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, তার ঠিকঠিকানা নেই। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি সবাই কেন হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যানুরাগী হয় না। আমার ধারণা হয়েছিল, হরিশ্চন্দ্র নাটকের গল্প বর্ণে-বর্ণে সত্য। সত্য পথে চলা ও সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার আদর্শ আমায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করত। হরিশ্চন্দ্রের কথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সহজ বুদ্ধি আজ আমি বেশ বুঝতে পারি, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনেও হরিশ্চন্দ্র ও শ্রবণ আমার কাছে যেন জীবন্ত মানুষ। আমি বেশ বুঝতে পারি, এই বয়সেও যদি আমি ওই দুটি নাটক পড়ি, ঠিক ছেলেবেলার মতো অভিভূত হয়ে পড়ব।” গান্ধিজি অনৈতিহাসিক হরিশ্চন্দ্রকে, -হরিশ্চন্দ্রের জীবনের সত্যকে আপন জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রবণ ও হরিশ্চন্দ্র তাঁর জীবনের গভীরে এক গভীরতর সত্যের জীব বপন করেছিল। সত্য ও সত্যের জন্য ত্যাগের আদর্শ মহাত্মাগান্ধি বাল্যকালেই শ্রবণ ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি থেকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন।
উপরোক্ত দৃষ্টান্ত গুলো তো বেশ আগের। কিন্তু আমাদের সময়ে অর্থাৎ মোবাইল, ফেসবুক, ইউটিউব এগুলো তখনও তাদের সা¤্রাজ্য বিস্তার করে বসেনি। সে সময় প্রত্যন্ত অ লের মফস্বল শহরগুলোতে, ঢাকা তো বটেই এমনকি গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বই পড়া, নাটক দেখা, নিজে নাটক লিখে সে নাটক ম স্থ করা কিংবা বিবিধ পালা-পার্বনে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার প্রবণতা ছিলো চোখে পড়ার মতো। আমি ও আমার মহল্লা কিংবা বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা মিলে চাঁদা তুলে ১৬ ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চ ও পহেলা বৈশাখ প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলোকে উপলক্ষ করে দেয়ালিকা কিংবা সাহিত্য পত্রিকা বের করতাম। আমরা বন্ধুরা’সব সমস্ত রাত জেগে হাতে লিখে সে সব দেয়ালিকা লিখনের কাজগুলো করতাম। আমার বাবা ছিলেন সত্যানুরাগী, সাহসী, দয়ালু কিন্তু অসম্ভব ক্রোধপরায়ণ একজন মানুষ। আমার স্কুল কলেজ জীবনে মাগরিবের আযানের পর এক মুহুর্তও ঘরের বাইরে থাকার উপায় ছিলো না। বাবার কড়া হুকুম- যেখানেই যাও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ফিরতে হবে। আমার সেই রাগি বাবা শুধুমাত্র সুকুমারবৃত্তিচর্চার জন্য সমস্ত রাত ঘরের বাইরে কাটানো অনুমদন করতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষগণও ছাত্রদের বই পড়ায় দারুন উৎসাহ দিতেন। আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা বলি। আমি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। অন্যান্য সব বিষয় ভালো লাগলেও অংক সাবজেক্টের প্রতি ছিলো আমার দারুন অনিহা। সেই অনিহা আজও বিদ্যমান আছে, সে হোক জীবনের অংক কিংবা টাকার অংক। সাধারণত অষ্টম শ্রেণিতে অংক ক্লাসটি নিতেন বাবর আলী স্যার, কিন্তু কোন কারণে সেদিন তিনি স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। ক্লাস নিতে এলেন রমেশচন্দ্র হালদার নামে জনৈক শিক্ষক। অন্যান্য সময় আমি বেে র প্রথম সারিতে বসলেও অংক ক্লাসের সময় আমি একেবারে পিছনের বেে বসে গল্পের বই পড়তাম। তো সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছি। হঠাৎ রমেশ স্যার হাতের ডোরাকাটা জালি বেত দিয়ে আমার মাথায় আলতো করে স্পর্শ করলেন। আমি মাথা তুলে তাকাতেই ভয়ে শরীর কেঁপে উঠলো। আমার ভয়ার্ত মুখ দেখেই হয়তো স্যার ঈষৎ অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এতো মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস। আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজেই বেতের ডগা দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টে দেখলেন আমি রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দা পড়ছি নিবিষ্ট চিত্তে। তিনি আমাকে কিছু না বলে যথারীতি ব্লাকবোর্ডে গিয়ে অংক শেখাতে লাগলেন। অল্পশোকে কাতর আর অধিকশোকে পাথর। আমার মনে হলো রমেশ স্যার অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছেন বোধহয় আর এ জন্যই হয়তো তিনি আমাকে কিছু বললেন না। ক্লাস শেষে তিনি আমাকে বললেন- চল আমার সঙ্গে অফিসরুমে। আমি তো ভয়ে অস্থির। অফিসরুমে নিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই আচ্ছাতারে শায়েস্তা করা হবে আমাকে। আমি মন্থর পায়ে অনুসরণ করলাম তাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসার কক্ষটির একপাশে চার-পাঁচটা আলমারি ভর্তি বই। আরশোলার পাখার রঙের মেহগনি কাঠের আলমারির দরজা খুলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- দেখ কত বই। ওখান থেকে ইচ্ছেমত তুলেনে দু’চারটে। আমি দেখলাম রবীন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিম, শরৎ সব থরে থরে সাজানো। আমি তুলে নিলাম রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ বইটি। রমেশ স্যার বললেন- তোকে যে বই পড়তে দেখলাম সে বিচারেই বলছি, পঠনের দিক দিয়ে তুই এখনো বেশ ‘নাবালক’। একলাফে তো আর সাবালক হওয়া যায় না। বইয়ের সারিগুলো থেকে তিনি আমাকে বের করে দিলেন ‘স্পেনে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস’। বইটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন- আগে এটা পড়। ভালো লাগবে। আর এখন থেকে বই লাগলে আমার কাছে চলে আসবি। বই পড়া খুব ভালো অভ্যাস কিন্তু অবশ্যই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নয়। এভাবেই রমেশ স্যার উসকে দিয়েছিলেন আমার বই পড়া। সেই সঙ্গে বই পড়ায় সাবালকত্বও লাভ করেছিলাম তাঁর বদৌলতে।
সাইফুর রহমান
গল্পকার ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী
বিষয়: সাইফুর রহমান

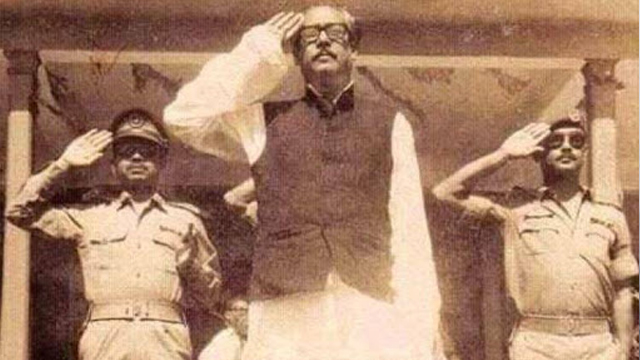




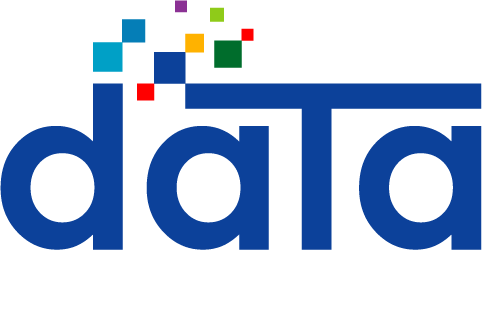
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: