দিলারা হাশেমের আমলোকীর মৌ: ব্যক্তিস্বাধীনতার বয়ান : আফরোজা পারভীন
প্রকাশিত:
১৮ মে ২০২১ ২০:৩১
আপডেট:
১৮ মে ২০২১ ২০:৫৩
দিলারা হাশেম একজন খ্যাতিমান বাংলাদেশী কথাসাহিত্যিক। তিনি ১৯৩৬ সালের ২১ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বি. এ. অনার্স ও ১৯৫৭ সালে এম. এ. সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস "ঘর মন জানালা" ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। ঘর মন জানালা পাঠক ও সমালোচক মহল কতৃক সমাদৃত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থটি রুশ ও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর নারীবাদী উপন্যাস “আমলকীর মৌ।” ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে কাজ করে ২০১১ সালে অবসর নেনন
১৯৭২ সাল থেকে লেখক আমেরিকার ওয়াশিংটনে প্রবাসী জীবন যাপন করছেন। প্রবাসে থাকলেও শেকড়ের টান অক্ষুন্ন রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলা সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছেন তিনি। যার স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তর আমেরিকা কবিতা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে ১৯৯৪ সালে ‘শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার’ এবং ১৯৯৭ সালে শিকাগোর ‘কালচারাল এ্যান্ড লিটারারি ইঙ্ক’ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।
ষাট এবং পরবর্তী সময়ের পথিকৃৎ উপন্যাসিক দিলারা হাশেম। শিল্পসত্তায় সমৃদ্ধ একজন সাধক তিনি। ব্যাপক তাঁর সৃজনকর্ম। এমন গুণীজনের পরিচিতিও ব্যাপক এবং সর্বজনবিদিত। পাঠকমাত্রই তাঁর নান্দনিকতায় মুগ্ধ, বিমোহিত। শুধু শৈল্পিক অনুরণনই নয়, সমকালীন সমাজ, সংস্কার, গতানুগতিকতাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লালন করা এই বিদগ্ধ উপন্যাসিক নারীর অধিকার ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ। তিনি মূলত তাঁর রচনায় নগর জীবন ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার ছবি তুলে আনেন।
ইটালী, ফ্রান্স, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়াসহ ইউরোপের বহু দেশ ও চীন, জাপান ও কমিউনিস্ট শাসনামলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করেন তিনি। এসব সফরের ফলে লেখকের রচনায় চরিত্র ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র দৃশ্যমান হয়। যা পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে: ঘর মন জানালা (১৯৬৫), একদা এবং অনন্ত (১৯৭৫), স্তব্ধতার কানে কানে (১৯৭৭), আমলকির মৌ (১৯৭৮), বাদামী বিকেলের গল্প (১৯৮৩), কাকতালীয় (১৯৮৫), মুরাল (১৯৮৬), শঙ্খ করাত (১৯৯৫), অনুক্ত পদাবলী (১৯৯৮), সদর অন্দর (১৯৯৮), সেতু (২০০০), মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমূহ (২০১১)
আছে গল্পগ্রন্থ: হলদে পাখির কান্না (১৯৭০), সিন্ধু পারের উপাখ্যান (১৯৮৮), নায়ক (১৯৮৯)। রয়েছে কবিতাগ্রন্থ ফেরারি (১৯৭৭)।
দীর্ঘ ৩৫ বছর ভয়েস অফ আমেরিকার বেতার ভাষ্যকার, সাংবাদিক হিসেবে কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়ে ৩১শে মার্চ ২০১১ সালে কথাশিল্পী দিলারা হাশেম অবসর নেন। বিদায়কালে তিনি বলেন,
‘যা কিছু করতে পারিনি এই দীর্ঘ জীবনে, কিন্তু করতে চেয়েছি, সেগুলোই এখন আঁকড়ে ধরবো’। বিদায়ী সাক্ষাৎকারে তিনি কিছু উজ্জ্বল মুহূর্ত স্মরণ করে বলেন, ‘এই কাজে পূর্ণ সময়ের জন্য যোগ দেওয়ার পর আমার প্রথম দায়িত্ব হয়েছিল দুটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান করার। আমেরিকার জীবনধারা ও কান্ট্রি মিউজিকের আসর। তো এই দুটো অনুষ্ঠান করার জন্য আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। ভয়েস অফ আমেরিকা থেকেই আমাকে পাঠানো হয় কান্ট্রি মিউজিকের পীঠস্থান ন্যাশভিলে। বেশ কয়েকবার সেখানে গিয়েছি বার্ষিক অনুষ্ঠান কভার করতে। সেখানে বহু শিল্পীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে, ব্লু গ্রাস সঙ্গীতের নামী শিল্পী বিল মনরোর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ওয়াশিংটনে জোন বায়েজের আত্মজীবনী, এ্যা ভয়েস টু সিং বইটির প্রকাশনা উৎসবে তার সঙ্গে দেখা হয়। উনি তার বইতে রবিঠাকুরের যে কবিতা রয়েছে, তার অংশ বিশেষ পড়ে শুনিয়েছিলেন, সেটা আমার কাছে চমৎকার লেগেছিল। তার সাক্ষাতকারভিত্তিক সেই অনুষ্ঠান ভয়েস আমেরিকার পুরস্কার পেয়েছে’।
বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, সরোজিনী নাইডু স্বর্ণপদক, অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার, কালচারাল এন্ড লিটারারি পুরস্কারসহ বহু সম্মানে ভূষিত দিলারা হাশেম অবসর জীবনে লিখবেন, গান গাইবেন, ছবি আঁকবেন, এতদিন যা করতে পারেননি এবার সেদিকে মন দেবেন বলে জানান।
এক সময় সঙ্গীতের প্রতি অনুরোক্ত ছিলেন দিলারা হাশেম। অল্পবয়স থেকে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন।
দিলারা হাশেম সময় এবং প্রচলিত ধারাকে অনুধাবন করে তাঁর সৃষ্টিযজ্ঞে দেশ, মানুষ আর মাটির সন্ধানে নিজেকে বিলিয়ে দেন। সমাজ এবং ইতিহাস তাঁর সাহিত্যের বিশাল সম্পদ। শিল্পিত অনুভবে নান্দনিকতার অপার সম্মোহনী মন্ত্রজালে বাস্তবের কষাঘাতও পড়ে তাঁর লেখায়। তিনি সময়ের গতি প্রবাহে যেমন নিজেকে প্রবাহিত করেন তেমনই প্রথাসিদ্ধ সমাজের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবেও কাজ করেন। সেটা করতে গিয়ে নারী জাতির শৈল্পিক সত্তা আবিষ্কারে তিনি মগ্ন হন। নারীর প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতায় তাদের প্রতি সচেতন হন। বৈষম্য পীড়িত এই গোষ্ঠীর সমঅধিকার আদায়ে সোচ্চার হন। নারীকে প্রতিদিনের যাপিত জীবনের দুঃসহ দুঃখ কষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়। নারীর ভাগ্যজয় করা হয় রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। যেখানে যাপিত জীবনই দুর্বহ। নারীর স্বপ্ন দেখা বারণ। কিন্তু লেখক চেয়েছিলেন নারী সদর্পে পথ পরিক্রমা করুক, গড়ে নিকে তাদের ভাগ্য। এটা সময় ও যুগের দাবি। আর তাই লেখকের উপন্যাসের নায়িকারা জীবন যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে আটকে পড়ে বটে, কিন্তু তলিয়ে যায় না। বাধা পায়ে দলে সংগ্রামী অভিযাত্রায় পথ পাড়ি দেয় তারা। সংস্কারাচ্ছন্ন মায়েদেরকে সমস্ত কূপমন্ডুকতাকে অস্বীকার করতে প্রাণিত করেন লেখক। শিল্পিত চর্চার বিচিত্র অনুভব জাগিয়ে তোলেন তাদের মনে। বাল্যকাল থেকে অসম অধিকার নিয়ে বড় হওয়া মেয়েদের গন্ডিতে বেধে দেয়া হয়। সেই নির্দিষ্ট গন্ডি থেকে বের হয়ে আসতে দ্বিধায় ভোগে তারা। সাহসে কুলোয় না তাদের। হিমশিম খায়। লেখক তাঁর লেখায় মেয়েদের সেই সব সীমারেখা, সব গন্ডিকে অদম্য সাহসে, মানসিক শক্তিতে পার হয়ে আসতে বলেন। এ সীমানা পার হতে না পারলে নিজেদের টিকিয়ে রাখা মুশকিল এটাও মেয়েদের জানিয়ে দেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে।
‘আমলকীর মৌ’ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই লেখা একটি উপন্যাস। চরম অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার সময়কালে উপন্যাসটি রচিত। তবে এর পটভূমি রাজনীতি নয়। রাজনীতি অর্থনীতি যেমন জনজীবনকে জড়িয়ে রাখে তেমন এ উপন্যাসেও অনিবার্যভাবে রাজনীতি এসেছে। তবে ঔপন্যাসিক দিলারা হাশেম চেষ্টা করেছেন কৌশলে ঐ সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে সামাজিক-পারিবারিক জীবনকে উপজীব্য করে তুলতে। তবু চেষ্টা করলেও পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে যারা নিশ্চিন্ত ছিলেন তারা কিছুটা নাড়া খান এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে। লেখক তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন দেশমুক্তির যুদ্ধ শেষ হয়েছে, নারী স্বাধীনতার যুদ্ধের মিমাংসা হয়নি। অর্জিত হয়নি মানবতার মুক্তি। সে যুদ্ধ চলমান। দেশ স্বাধীন হলো। নারী স্বাধীন হলো না। মুক্ত আর উদার হলো না সমাজের বোধ-বুদ্ধি মানসিকতা। তাই লেখকের মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়। এসব প্রশ্ন নিয়েই হাজির হলো ‘আমলকীর মৌ’। দিলারা হাশেম উপন্যাসে সৃষ্ট কিছু চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন, পুরুষের সৃষ্ট মূল্যবোধ নিয়ম-নীতি, আইন-কানুনে আপাদমস্তক জিম্মি নারীরা। এ সমাজ ব্যবস্থা নারীবান্ধব নয় বরং মারাত্মক প্রতিবন্ধক। জিম্মি একশ্রেণির পুরুষও। যাদের টাকা নেই, হাতে ক্ষমতা নেই। যুদ্ধ পরবর্তীকালে ক্ষমতা আর টাকা তাদের হাতেই এসেছিল যারা রাজনীতি করতেন, রাজনীতির সাথে ছিলেন। তাই উপন্যাস থেকে মোটেও রাজনীতিকে বাদ দেয়া গেল না। ‘আমলকীর মৌ’ চরমভাবে রাজনৈতিক একটি উপন্যাস। এ উপন্যাসে একজন নারী গেরিলা যোদ্ধার মতো জীবনযুদ্ধ করেছেন। সেই যুদ্ধকে কোনভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। সে যুদ্ধ বিশাল।
‘আমলকির মৌ’ নারীকেন্দ্রীক উপন্যাস। নারীকেন্দ্রীক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আরও অনেক লেখা হয়েছে। তবে এরকম সাহসী উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম। সত্তর দশকে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক নারী স্বামী-সন্তান ছেড়ে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে বাস করছে। রাত নেই দিন নেই রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। ইচ্ছে হলে পান করছে তরল কিংবা ধূম। ব্যাচেলর বন্ধুর ফ্লাটে ঢুকে পড়ছে যখন তখন এমন একটা চরিত্র এঁকেছেন লেখক। সত্তর দশক কেন, এসব ভাবতে এখনও অনেক মেয়ের গা শিউরে উঠবে। আমাদের প্রচলিত মননে একজন বিবাহিত নারীর জীবন যেমন হওয়ার কথা তা উচ্চবিত্ত হোক বা নিম্নবিত্ত তার সাথে সারার জীবন মেলে না। তা যতই উচ্চশিক্ষিত আর আত্মবিশ্বাসী হোক না কেন। একই সাথে এটাও ঠিক সারার মতো আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমতী ও উচ্চশিক্ষিত, চমৎকার ইংরেজি বলা নারী চরিত্রও বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি নেই। সারা রূপসী ও বিদূষী। এই রূপগুণই তার কাল হয়েছে নিজের জন্য, অন্যের জন্যও। নারী রূপসী হবে ঠিক আছে। কিন্তু নারীর গুণ থাকা যে পুরুষালি! যে গুণ শুধু পুরুষেরই থাকার কথা তা নারীর থাকবে কেন? এটা সারার দোষ। সারা যোগ্য। তার আচরণ যোগ্য মানুষের মতো। সে পুরোনো জংধরা নারীবিদ্বেষী সমাজকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়তে চেয়েছে। সম্পূর্ণ না পারলেও সমাজের কিছু মানুষকে অন্তত সে বুঝাতে পেরেছে, এভাবেও নারীরা বেঁচে থাকতে পারে। এবং এভাবেই বেঁচে থাকা উচিত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজিতে মাস্টার্স এবং বিদেশ থেকে ডিগ্রি নেয়া সারা। সে ইচ্ছে করলেই তার রূপ গুণের বদৌলতে অন্যরকম একটা জীবন পেতে পারতো; সে তা করেনি। রূপচর্চা ও স্টাইল নিয়ে সে ভাবে না। সে বোঝে ওগুলো নারীর অস্তিত্ব বিরোধী। নারীকে আরও নারী করে তোলার চেষ্টা। ‘উপকরণ হিসেবে সে কোনমতেই ব্যবহৃত হবে না, এক্সপ্লয়টেডও নয়।’ [পৃ.১২, ‘আমলকীর মৌ’, মুক্তধারা, ১৯৭৮] এটা সে সচেতন ভাবেই ভাবে। বরং প্রয়োজনে সে নিজেই পুরুষদের ব্যবহার আর এক্সপ্লয়টেড করতে চায়। সারা তার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে বন্ধুদের উপকার করে বেড়ায়। বলা চলে বন্ধুরা তাকে ব্যবহারই করে। সারা বিষয়টা বোঝে না এমনও না। বুঝেও সে এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বন্ধুদের উপকার হচ্ছে, এটা ভেবেই খুশি সারা।
সারা সবসময় সংসারের নানান অনিয়মের প্রতিবাদ করে। অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। এ অনিয়ম আর সে প্রশ্নগুলো আমরাও জানি। কিন্তু কখনও তলিয়ে ভাবিনি। সারার প্রতিবাদ আমাদের ভাবায়। তার প্রশ্ন থেকে রেহাই পান না নিজের বাবাও। ‘যে লোকটি দিনের বেলায় আম্মা মানুষটার সাথে প্রায় সম্পর্কবিহীন দিন কাটায়, সে রাতে কোন সম্পর্কের দাবিতে এবং কিভাবে অতগুলি সন্তানের পিতৃত্বের অধিকারী হয়!’ [পৃ.২৩] সংসারে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা যে কতো জোলো তা সারার প্রশ্ন থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সারা তার বাবা-মার মধ্যকার অস্বচ্ছ দাম্পত্য সম্পর্ক দেখে। আর এই দেখার ভেতর থেকে সমস্ত নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভেতর অস্বচ্ছতা দেখতে পায়। আর তাই সে পারে তার স্বামী-সন্তান ফেলে চলে আসতে। হ্যাঁ অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী না হলে হয়ত সে পারত না। কারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অর্থের প্রয়োজন। সারার স্বামী সন্তান ফেলে আসার সাহসের পেছনে শক্তি জোগায় তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা। সারার বোন সালেহার স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল না। সে স্বামীকে ছেড়ে চলে আসতে চেয়েছিল। সালেহা আশ্রয় চেয়েছিল বাবার কাছে। বাবা সম্মান ও সমাজের ভয়ে তাকে আশ্রয় দেননি। সালেহাকে জোর করে ফেরত পাঠাতে পেরেছিলেন তিনি। সংসারে ধরে রাখতে পারেননি। সালেহা সারার মতো নিজ ইচ্ছায় চলতে পারেনি কারণ তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। কারণ সে সারার মতো অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী নয়। তাই জাগতিক মুক্তির বদলে তাকে চিরন্তর মুক্তির পথ বেছে নিতে হয়। সে আত্মহত্যা করে। আসলে নারী স্বাধীনতায় জন্য নিজস্ব আয় যে কতটা জরুরী এ উপন্যাস সে কথা আর একবার বলে দেয়। ভার্সিনিয়া উলফ নারীদের জন্য নিজস্ব একটা কামরা চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা বলে দেয় নারীদের জন্য শুধু নিজস্ব কামরা নয়, নিয়মিত কিছু অর্থ উপার্জনও প্রয়োজন। নারী ক্ষমতায়ন বা স্বাধীনতার সাথে জড়িয়ে আছে অর্থনীতি। মার্ক্স বলেছেন, ‘একটা ক্লাশ ইকোনোমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কখনই খাঁড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না’। এই অমোঘ বাণী সত্য নারীদের ক্ষেত্রেও।
সারার বাবা আজম খান উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষ। তার সময় কাটে বই পড়ে নয়ত সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে। কি ইতিহাস, কি দর্শন, কি রাজনীতি সবকিছুতেই তিনি সমান পন্ডিত। তার সবসময়ের সঙ্গী হলেন কান্ট, হেগেল, গেটে, স্পিনোজা, প্লেটো, রাসেলের মতো বিশ্ব পন্ডিতরা। পন্ডিত হয়েও আজম খান সমাজের মানবতাবিরোধী নিয়মের হাতে বন্দি। নিয়মকে তিনি অবজ্ঞা তো করেনই না, অবজ্ঞা করার কথা ভাবেনও না। কাজের মেয়ের সাথে বড় ছেলের প্রণয়ের ঘোর বিরোধী তিনি। কৌশলে নিজের এক কর্মচারীর সাথে ঐ মেয়ের বিয়ে দিয়ে অন্যত্র বদলি করে দেন। সালেহা অত্যাচারী-বহুগামী স্বামী রশীদের সংসারে ফিরে যেতে না চাইলেও আজম খান সমাজে সম্মান হারানোর ভয়ে তাকে যেতে বাধ্য করেন। কিছুদিন পর সালেহা আত্মহত্যা করে তা আগেই বিবৃত হয়েছে। এ মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ান আজম খান। আজম খান শিক্ষিত হয়েও নিজের সবচেয়ে কম সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগেন। সমাজে তার বাজার দর কম, এ বিষয়টা তিনি মনে গেঁথে রাখেন সবসময়।
আবার নারী শিক্ষিত সচেতন সাহসী আর তার অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হলেই একক প্রচেষ্টায় সমাজের বিশ্বাস আচারকে বদলানো যায় না। মেয়েরা মৃতের খাটিয়া বহন করতে পারে না। এ নিয়ম কবে কখন কে করেছিল তা জানি না। তবে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। তাই সারা তার খালার খাটিয়া ধরতে চাইলে মামা বলেন, ‘তুই বয়ে নিয়ে যাবি? তুই তো মেয়ে মানুষরে। মুর্দায় কাঁধ দিতে গেলে পুরুষ হতে হয়। ওটা তোর কাজ নয়।’ [পৃ.২৮] একা সারা কি করে এ নিয়ম ভাঙবে! এখানে এসেই তাই আটকে যায় সারা।
সারার চালচলন, আচার ব্যবহার তাকে পরিবার ও সমাজের কাছে ‘মোস্ট আন-ওয়ানটেড’ করে তোলে। কিন্তু রাতের আঁধারে চিত্র বদলে যায়। তখন সেই হয়ে ওঠে এই সমাজেই সবচেয়ে ‘ওয়ান্টেড’। সারার কাছে পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ পরিষ্কার হয়ে যায়। সংসারে যারা ভাল স্বামী, নিজেদের স্ত্রীর ব্যাপারে তারা প্রটেকটিভ। আগলে আগলে রাখে স্ত্রীকে। তারাই পরনারীতে বেশি আসক্ত। সমাজ সারাকে কটাক্ষ করে বলে, ‘মেয়েটার লজ্জা বলে কি কিছু নেই?’ কারণ সে বাইরে থাকে রাত বিরেতে। নিজের ইচ্ছেমাফিক চলাফেরা করে। পরিবার সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় সারাকে। পরিবারের নারীরাই সারার বড় শত্রু। মা, বড় বোন, ভাবি, বোনের মেয়েরা পর্যন্ত। কেউই সারার স্বঘোষিত স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। ছোট বোন নীলু সারাকে বলে, ‘তোমার মত মেয়ের বাবা বলে পরিচয় দিতে আব্বার লজ্জা করবে।’ [পৃ.৫০] মা যোগ করেন, ‘মেয়েটার লজ্জা বলে কি কিছু নেই?’ [পৃ.৫১] বড় আপা মেয়ের চুল কাটার বিষয়ে বলে, ‘হাঁটু-ধরা চুল নইলে চলবে কি করে, বর জুটাতে হবে না?’ [পৃ.৫২] পিতৃপরিচয় যে সমাজে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিও সারাকে বুঝিয়ে দেন বড় আপা, ‘পিতা যে আছেন, সেটুকুও কম কথা নয়রে। আছেন তাই টের পাচ্ছিস না। যেদিন সত্যিই থাকবেন না, সেদিন বুঝবি। নামটারও ত কিছু মাহাত্ম্য আছে।’ [পৃ.৫৬] ভাবী সেজেগুঁজে স্বামীর বন্ধুদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর থাকে, অথচ সারার কোন বন্ধু বাড়ি পর্যন্ত এলেই মহা সর্বনাশ। চোখ জ্বালা করে সবার। এ সংসারে ‘স্বামীর বন্ধু হলেই সাত খুন মাফ।’ [পৃ.৫৮] যেন সংসারে নারীর কোন বন্ধু থাকতে নেই। নারীরা সেটা মেনেও নিয়েছে, সারা মানেনি। তাই তার সমস্যা। অন্যদিকে অন্ধকার রাতে সারা কারো ডাকে সাড়া না দিলে, কারো সাথে বিছানায় যেতে রাজি না হলে সেই সমাজই আবার সারাকে ‘কনজারভেটিব’ আখ্যায়িত করে বলে, ‘ইউ ডোন্ট নীড টু স্লীপ উইথ এভরি আদার বয় ইউ মীট, বাট ইউ মে স্লীপ উইথ ওয়ান অর টু – ইউ লাইক মোস্ট। কাম অন সারা, শরীর ছুঁলেই তোমার প্লেগ হয়ে যাচ্ছে না।’
সারা প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়ে না করে সে কারো সাথে শোবে না। সে ইচ্ছেমতো চলে। ইচ্ছে হলে পান করে, না হলে না। সে সবকিছু করে সম্পূর্ণ নিজের জন্য। কারও মনোঞ্জন করার জন্য না।‘একমাত্র নিজের অন্তরের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহির জন্য সে প্র¯ুÍত নয়।’ [৪৯] এমন চরম অস্তিত্ব সচেতন নারী বাংলা সাহিত্যে বিরল।
প্রতিদিনই তাকে ঘরে বাইরে কটুক্তি শুনতে হয়। সারা কখনও প্রতিবাদ করে, কখনও করে না। তবে তাদের কথায় নিজের জীবনের ছক থেকে তিল পরিমাণ নড়চড় হয় না। এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ।
সারা একজন নারী হিসেবেই সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। একজন পুরুষের জন্য যদি পুরুষ পরিচয়ই যথেষ্ট হয়, তবে কেন নারীকে আলাদা করে মানুষ হয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে? অলরেডি সে একজন নারী, এবং এইটাই সারার জন্য যথেষ্ট।
কিন্তু সারা যখন বলে, ‘আই উইল ম্যারী এগেইন। আই মাস্ট গেট আউট অব ইট।’ তখন আমরা হোচট খাই, ঘাবড়ে যাই। প্রশ্ন জাগে মনে, সারা আসলে কোথা থেকে বেরুতে চাইছে? মুক্তির জন্য সে আবার বিয়ের কথা ভাবছে কেন? কেন মুক্তির পথ হিসেবে সে বিয়েকে বেছে নিচ্ছে? কোনো পুরুষ তো মুক্তির জন্য বিয়ের কথা ভাবে না। উপন্যাসের শেষের দিকে এসে সারাকে তিনি নারীদের থেকে আলাদা করলেন, আবার সারাকে করে তুললেন সবচেয়ে পুরুষনির্ভর। নইলে সে শুরুতে দারা, পরে বন্ধু হাসিব, প্রেমিক ফিরোজ এবং সবশেষে বড় ভাই মতিন-এর ওপর এত বেশি নির্ভর করবে কেন! তাই নারী স্বাধীনতার কথা বললেও শেষাবধি নারী স্বাধীনতার একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন রেখে গেছে ‘আমলকীল মৌ’ উপন্যাসটি।
উপন্যাসের অধিকাংশ পুরুষ নারীর প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। সারার বড় ভাই সকিনাকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারেনি বলে জীবনে আর কোন নারীর সংস্পর্শে আসেনি। চরিত্রে ত্রুটি নেই সারার বাবা এবং অন্য দু’ভাইয়ের। হাসিব সারাকে ভালবাসে। সে সারাকে দেহ-মন দিয়ে কামনা করে, অথচ সারা একা তার বাসায় রাত কাটালেও সে সারাকে অমর্যাদা করে না। ফিরোজ সুযোগ পেয়েও সারার শরীর পর্যন্ত এগোয় না। সারার বন্ধু সাজিদ সারার কাছে অন্যায় আবদার করলেও সারার মর্যাদাহানি সে করেনি। সারার বড় ভগ্নিপতী ছিলেন অতি ভালমানুষ। সালেহার স্বামীর মতো দু-একজন লম্পট আছে উপন্যাসে। তাদের ভূমিকা খুবই খাটো। এ বিষয়টি কতটা বাস্তব সেটা ভেবে দেখার।
সমাজে দ্বৈত মানদন্ডে নারীর মূল্যায়নে দৃপ্ত প্রতিবাদী ‘সারা’ চরিত্র। জীবনে প্রবঞ্চিত, প্রতারিত হয়ে সালেহারা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সাকিনারা নির্যাতিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে। কিন্তু সারা জীবনের বঞ্চনাকে দু’পায়ে দলে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সংগ্রামে ঋজু, আত্মপ্রত্যয়ে অনমনীয়, প্রতিবাদে প্রখর, মমতায় মহীয়সী সে। দুর্বার মনোবল নিয়ে সমাজের বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়ার সংগ্রামে ব্রতী হয় সারা। সমাজে নির্যাতিত, অবহেলিত, প্রতারিত হাজার নারীকে মাথা তুলে দাঁড়াবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে যেমন নারী প্রয়োজন সেই নারীর প্রতিভূ সারা। তার তিক্ত,বিষাদিত অম্ল মধুর জীবনেরই আলেখ্য “আমলকির মৌ।”
কিন্তু উপন্যাসের শেষদিকে এসে যেন সাজানো সবকিছু খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। মৃত্যু বা চরম বিচ্ছেদের ভেতর দিয়ে সম্পর্কগুলো কাছাকাছি আসে, সবচেয়ে আপন হয়ে ওঠে। সারার মায়ের মৃত্যু, মেজো বোনের আত্মহত্যা, প্রেমিক ও বাগদত্তা ফিরোজের মৃত্যু; বড় ভাইয়ের প্রেমিকা সকিনার আত্মহত্যা, এতগুলো মৃত্যু বদলে দেয় উপন্যাসের চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক। মৃত্যুগুলি উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উপন্যাসের শেষে এসে নিয়মভাঙা মেয়ে সারা কপাল বা অদৃষ্টের লিখনকে বিশ্বাস করতে থাকে। সে বলে, ‘অশ্রু ঢেলেই ফুল ফোটানো যে আমার ভাগ্য, সে আমি এড়াবো কেমন করে? আমি যে আমলকীর মৌ।’ [পৃ.৩৫৮]
প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসে লেখকের সমান মনোযোগ দাবি করা উচিত নয়। উপমার ক্ষেত্রে উপন্যাসিক বার বার প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। উপন্যাসের শুরু ও শেষটা হয়েছে প্রকৃতির হাত ধরে।
শুরু: ‘রাস্তার দুপাশে ডালপালা ঝাঁপানো গাছগুলো যে পাতার মশারি। পথটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে আর সেই মশারির জালি ছেঁকে ঝরে পড়ছে জোছনার রেণু। সেই জোছনার আফসা গায়ে মেখে বড় বড় সেগুন পাতাগুলো বেদেনী মেয়েদের মত হাওয়ায় শরীর নাচাচ্ছে। সেগুন ফুলের মৃদু মিষ্টি ঘ্রাণ যেন তাদের দেহের বাসনাময় মদিরতা। জোছনার সাজ পরে এই শহুরে রাতও পেয়েছে অভাবনীয় এক রূপের মাদকতা।’
শেষ: নদীর মত জীবনটা এখনও বইছে। কোন বড় ঝঞ্ঝায় এই বহমান জীবনের স্রোত কখনও থামতে জানে না। নিরবধি গতিই এর পরিণতি। এখনও ঋতু পরিবর্তন হয়। মুকুল ধরে ফুল ফোটে, চন্দ্র, সূর্য, তারা ওঠে আপন নিয়মে।’
ভাষার বিন্যাস ও উপমার প্রয়োগ কোথাও কোথাও কবিতার মতো। চরিত্রগুলির ডিটেলিং মনোমুগ্ধকর। কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রও ঘটনা বর্ণনার কারণে ঐ সময়ে জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
‘আমলকীর মৌ’ বাস্তববাদী উপন্যাস হলেও এই উপন্যাসে সারাসহ প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মনন জগতের পরিচয় মেলে। চরিত্রগুলির একান্ত অনুভূতিগুলোও পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন দিলারা হাশেম।
দিলারা হাশেমের এই উপন্যাসটা কোথাও কোথাও ঘটনানির্ভর আবার কোথাও কোথাও বক্তব্যনির্ভর।
দিলাশা হাশেমের ‘আমলকীর মৌ’ উপন্যাসে মূল কথক লেখক নিজেই, মাঝে মধ্যে কথকের ভূমিকায় চলে এসেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র সারা।
দিলারা হাশেমের ভাষা যথেষ্ট আবেগবর্জিত। ঘটনার বয়ানে তিনি যতটা নির্মোহ থাকা সম্ভব ততটাই থেকেছেন।
চরিত্রায়ন, বিস্তার, ভাষা ও উপমার ব্যবহার সবদিক থেকেই উপন্যাসটি একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। প্রতিটি চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তার বেশি জানার প্রয়োজন পড়ে না। ৩৮০ পৃষ্ঠার উপন্যাসে মোট বিয়াল্লিশটা অনুচ্ছেদ আছে। সব অনুচ্ছেদ আয়তনে সমান না। একেকটা অনুচ্ছেদে একেকটা গল্প রয়েছে। একটি মূল ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাবতীয় ঘটনার অবতারণা ঘটেছে। উপন্যাসের পটভূমি ঢাকা, সময় ৭০’র দশক। উপন্যাসের মূল কনফ্লিক্ট আপাত দৃষ্টিতে নারীর সাথে সমাজের মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সাথে সমাজের। আবার ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিরও। কোথাও কোথাও আবার নিজের সাথে নিজের।
সব মিলে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস যা সব কালেই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।
আফরোজা পারভীন
কথাশিল্পী, গবেষক, কলামলেখক
বিষয়: আফরোজা পারভীন

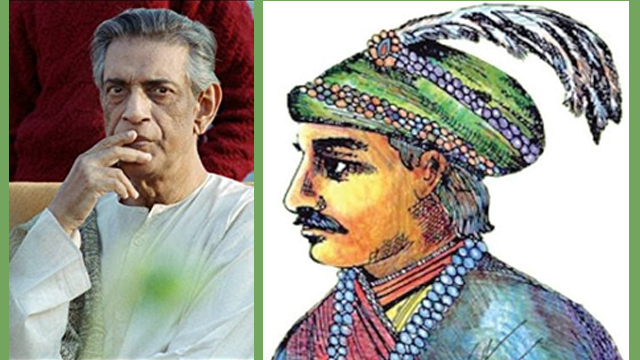
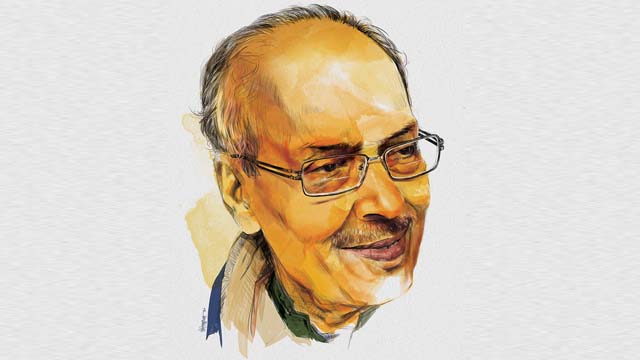



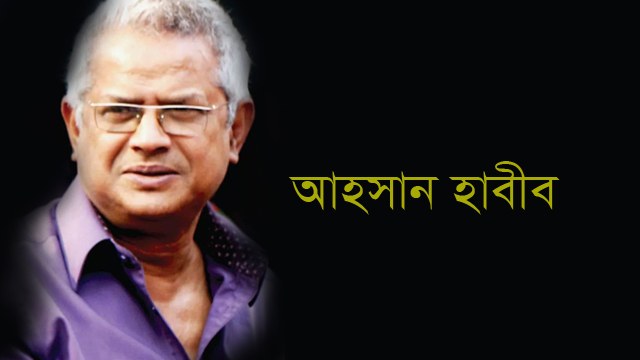


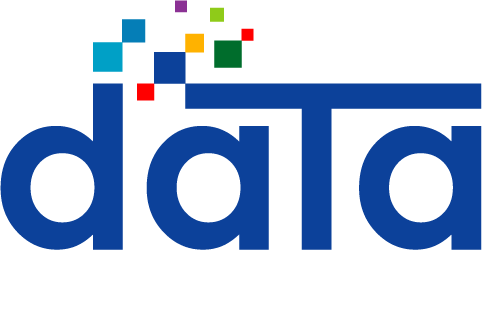
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: